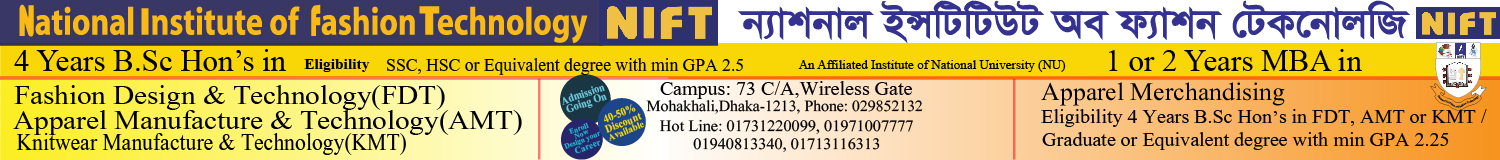জীবদ্দশায় কোনো পুরস্কার পাননি তিন বাঁড়ুজ্যের বিভূতি
সিদ্ধার্থ সিংহ
পশ্চিমবঙ্গের একসময়ের স্বনামধন্য মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কিংবদন্তি চিকিৎসক ও রাজনীতিবিদ বিধানচন্দ্র রায়। তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে, একটি গরিব ছেলে কীভাবে তার আনুকূল্য পেয়েছিল, সেই গল্পই ধরা পড়েছে, ‘একটি পেরেকের কাহিনী’-তে। আর এ রকম অসামান্য একটি কাহিনি লিখেও যিনি কেবল সম্পাদনায় মনোনিবেশ করবেন বলে লেখালিখি থেকে প্রায় হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন, সেই প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক সাগরময় ঘোষ বলেছিলেন, লেখক হতে গেলে বিশেষ করে তিনটি ক্ষমতার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, প্রচুর পড়াশোনা, মানে বিদ্যা-বুদ্ধি থাকা চাই। দ্বিতীয়ত, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। আর তৃতীয়ত হলো, কতখানি সিমেন্টের সঙ্গে কতখানি বালি মেশালে ইমারত গাঁথা যায়, সেই কলাকৌশলটুকুও জানতে হবে। অর্থাৎ কতখানি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কতটুকু কল্পনার মিশেল দিলে সেটা সাহিত্য হয়ে উঠবে, সে সম্পর্কে অবশ্যই টনটনে জ্ঞান থাকতে হবে।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে এই তিনটি গুণই একেবারে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৯৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার কল্যাণীর কাছে ঘোষপাড়া অঞ্চলের মুরারীপুর গ্রামে। তার মামার বাড়িতে। তার পৈত্রিক বাড়ি ছিল উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ মহকুমার ব্যারাকপুরে। বাবার নাম মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। মায়ের নাম মৃণালিনী দেবী। তাদের ছিল পাঁচটি সন্তান। তার মধ্যে বিভূতিভূষণই ছিলেন বড়।
তার বাবা ছিলেন সংস্কৃতের একজন নামকরা পণ্ডিত। সংস্কৃতে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তাকে শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। বিভূতিভূষণ তার বাবার কাছেই প্রথম পড়াশোনা শেখেন এবং নিজের গ্রাম আর আশপাশের গ্রামের বেশ কয়েকটা পাঠশালা থেকেও তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এর পর তিনি ভর্তি হন বনগ্রাম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে। সেখানে তিনি একজন অবৈতনিক শিক্ষার্থী হিসেবেই পড়াশোনা করেন।
ছোটবেলা থেকেই নিজের পড়াশোনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন ভীষণ মনোযোগী। সে জন্যই পরে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র। তার ছেলেবেলা কেটেছিল অভাব আর দারিদ্র্যের মধ্যে। তবে তার মনের মধ্যে তখনই লেখক হওয়ার বীজ রোপণ হয়ে গিয়েছিল, যখন তিনি সবেমাত্র পাঠশালায় যাওয়া শুরু করেছেন। পাঠশালায় কিছুতেই তার মন বসত না। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লেই তার বাবা তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালির জগতে। চলে যেতেন ইছামতির পাড়ে। এটা চেনাতেন। ওটা চেনাতেন। সেটা চেনাতেন।
একদিন তাকে নিয়ে বনমরিচের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রকাণ্ড এক গাছের কাছে এসে দাঁড়ালেন তার বাবা। তাকে বললেন, এই হলো সপ্তপর্ণ জুনিপার গাছ। বুঝেছিস? তোর দাদু এই গাছের বাকল দিয়ে ওষুধ তৈরি করতেন। আর আমি সেগুলো খুব ভালো করে ছেঁচে-বেটে দিতাম। বাবা চেনালেও মাঝে মধ্যে বিভূতিভূষণ নিজেও এই গাছ, ওই পাখি দেখিয়ে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করতেন, বাবা, এটার নাম কী গো?
এভাবেই একদিন তিনি একটা গাছ দেখিয়ে তার বাবার কাছে জানতে চাইলেন, বাবা এই গাছটার নাম কী? তার বাবা সঙ্গে সঙ্গে সেই গাছটির কাছে গিয়ে বললেন, সে কী রে! তোকে তো দুদিন আগেই এই লতাটা চিনিয়ে দিয়েছিলাম! ভুলে গেছিস! এই তো সে দিন তোর মায়ের গলা ভেঙে গিয়েছিল। এটার লতাপাতা থেঁতলে রস করে যেই তোর মাকে খাইয়ে দিলাম, অমনি তার গলা ভাঙা সেরে গেল। বিভূতিভূষণ বললেন, ওহো, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। তার মানে এটাই সেই অপরাজিতা গাছ?
এভাবে কিছু দিন চলার পর বিভূতিভূষণের হঠাৎ কী খেয়াল হলো কে জানে। নোটবুকের মতো একটি খাতা তৈরি করলেন এবং নতুন কোনো গাছ, লতা, পাখির নাম শুনলেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি পেন্সিল দিয়ে সেটা লিখে রাখতে লাগলেন।
সব ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু তিনি যখন ক্লাস এইটে উঠলেন, ঠিক তখনই মাত্র কয়েক দিনের রোগে ভুগে তার বাবা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। অগত্যা ছোট ছোট ভাইবোনদের নিয়ে তার মা-ও চলে গেলেন বাপের বাড়ি সুরাতিপুরে। কিন্তু পড়াশোনার জন্য রেখে গেলেন তার বড় ছেলে বিভূতিকে। তিনি তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৯১৪ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় তিনি ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করলেন এবং ভর্তি হলেন রিপন কলেজে। যেটার নাম এখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ।
তিনি বোডিংয়ে থাকতেন। তার বোডিংয়ের খরচ তখন চালাচ্ছেন সহৃদয় প্রধান শিক্ষক চারুবাবু। তিনি জানতেন, বিভূতি অতি মেধাবী ছাত্র। কিন্তু বিভূতিকে তিনি পছন্দ করতেন অন্য একটা কারণে। কারণ, বিভূতি নানা রকম বই পড়তে ভালবাসেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন, এই ছেলে জীবনে সফল হবেই। তার সুপারিশেই ডাক্তার বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যয়ের বাড়িতে তার খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা হলো। শর্ত একটাই, ডাক্তার সাহেবের ছেলে জামিনীভূষণ এবং মেয়ে শিবরানীকে তার পড়াতে হবে। বিভূতিভূষণ রাজি হয়ে গেলেন।
বিধু ডাক্তারের বাড়ির পাশেই মন্মথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। আর এই বাড়ির আকর্ষণ হলো এখানকার একটি ক্লাব, লিচুতলা ক্লাব। এই ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মন্মথ চ্যাটার্জি। তিনি মোক্তার হলেও আসলে মনেপ্রাণে ছিলেন একজন সাহিত্য সাধক। বিভূতিভূষণ বুঝতে পারলেন, মন্মথদা শুধু নিজেই সাহিত্য রচনা করেন না, ‘বালক’ এবং ‘যমুনা’ নামের দুটি সাহিত্য পত্রিকারও গ্রাহক। উনিও সেগুলোর অনুগ্রাহক হয়ে গেলেন। একেকটি সংখ্যা লিচুতলা ক্লাবে আসতে না আসতেই ছোঁ মেরে নিয়ে তিনি পড়া শুরু করে দিতেন। এই লিচুতলা ক্লাবে বসেই ‘যমুনা’ পত্রিকায় বার্মা প্রবাসী এক বাঙালি লেখকের একটি ধারাবাহিক উপন্যাস পড়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন তিনি। কে এই লেখক, যার নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? কী জাদুময় তার লেখনীশক্তি! সেও কি কোনো দিন পারবে এ রকম কোনো লেখা লিখতে?
এ ভাবেই লেখক হওয়ার দুর্বার আকর্ষণ তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকল। তবে বিভূতিভূষণের প্রথম লেখার সূত্রপাত হয়, যখন সে রিপন কলেজের ছাত্র। বিশিষ্ট সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তখন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ। তার প্রেরণাতেই কলেজে তখন পুরোদমে চলছে বিতর্ক সভা, সাহিত্যচক্র, সাহিত্যপত্র প্রকাশ। আর এই সাহিত্যচক্রের একটি অনুষ্ঠানে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ‘নতুন আহ্বান’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখে সেটি পাঠ করলেন বিভূতিভূষণ। সবার কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা ও সুখ্যাতি পেয়ে একদিন তিনি একটা কবিতাও লিখে ফেললেন। কলেজের ম্যাগাজিনে।
লেখালিখির পাশাপাশি তার পড়াশোনা চলছিল পুরোদমে। আই. এ পরীক্ষায় তিনি ফার্স্ট ডিভিশনে এবং ১৯১৮ সালে এই একই কলেজ থেকে বি.এ পরীক্ষায়ও ডিস্টিইংশন-সহ পাশ করেন। এর পর তিনি আইন নিয়ে পড়ার জন্য ভর্তি হন ঠিকই, কিন্তু কোর্সের মাঝপথে আর্থিক অনটনে তাকে পড়াশোনায় ছেদ টানতে হয়। এর পরে তিনি প্রথমে হুগলির জাঙ্গীপাড়ার দ্বারকানাথ উচ্চবিদ্যালয়ে এবং পরে সোনারপুরের হরিনাভির একটি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। দ্বারকানাথ উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ানোর সময় ১৯১৯ সালে বসিরহাটের মোক্তার, শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে গৌরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের ঠিক এক বছর পরেই গৌরী দেবী মারা যান।
সে সময় বউয়ের শোকে তিনি এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে, সেই চাকরি ছেড়ে শেষমেশ তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিটোলায় খেলাত ঘোষদের জমিদারির সেরেস্তায় নায়েবের কাজ নিয়ে চলে যান ভাগলপুরে। তিনি কিন্তু তখনও সে ভাবে লেখালেখি শুরু করেননি। এই ভাগলপুরেই ১৯২৫ সালে তিনি ‘পথের পাঁচালী’ লেখা শুরু করেন। মূলত নিশ্চিন্দীপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে। অপু আর দুর্গাকে নিয়ে। লেখাটা শেষ হয় ঠিক তিন বছর পরে। অর্থাৎ ১৯২৮ সালে। এটাই তার লেখা সব চেয়ে সেরা উপন্যাস।
এই উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে ও মোট পঁয়ত্রিশটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা। প্রথম খণ্ডটি হল, বল্লালী বালাই (পরিচ্ছেদ ১-৬; ইন্দির ঠাকরূনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে)। দ্বিতীয় খণ্ড, আম-আঁটির ভেঁপু (পরিচ্ছেদ ৭-২৯; অপু-দুর্গার একসাথে বেড়ে ওঠা, চঞ্চল শৈশব, দুর্গার মৃত্যু, অপুর সপরিবারে কাশীযাত্রা চিত্রিত হয়েছে)। এটাকে আবার পথের পাঁচালীর ছোটদের সংস্করণও বলা হয়। আর তৃতীয় খণ্ডটি হল--- অক্রূর সংবাদ (পরিচ্ছেদ ৩০-৩৫; অপুদের কাশীজীবন, হরিহরের মৃত্যু, সর্বজয়ার কাজের জন্য কাশীত্যাগ এবং পরিশেষে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে আসার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে)।
আর এই উপন্যাসের মধ্য দিয়েই তার লেখক জীবনের সূত্রপাত হয়। পথের পাঁচালী লেখার আগে অবশ্য ‘স্মৃতির রেখা’ নামে তিনি দৈনন্দিন খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যক্তিগত জার্নালের মতো কিছু একটা লিখতেন। তারও আগে ১৯২১ সালে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয়।
এই ভাগলপুরে তিনি যেমন পথের পাঁচালী লিখেছিলেন, ঠিক তেমনি এই ভাগলপুরেই উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নজরে পড়েছিলেন তিনি। দুটো ঘটনাই ছিল একেবারে রাজযোটক। সাহিত্যের ইতিহাসে এই উপেন্দ্রনাথ বিখ্যাত হয়ে আছেন দু'জন কিংবদন্তি সাহিত্যিককে আবিষ্কার করার জন্য। তাদের একজন হলেন এই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর দ্বিতীয় জন হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
কলকাতা থেকে আইন পাস করে উপেন্দ্রনাথ চলে এসেছিলেন ভাগলপুরে আইন ব্যবসার উদ্দেশ্যে। কলকাতায় লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সময়ই তিনি সাহিত্যের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওই সময়ের বিখ্যাত পত্রিকা ‘ভারতবর্ষ’, ‘সাহিত্য’সহ নানান পত্রপত্রিকায় তিনি লিখতেন। ওকালতি করতে এসে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তার ভাগলপুরের বাড়িতে তো বটেই, তার আশপাশেও একটি সাহিত্যের পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছিলেন। তিনি ছিলেন একদিকে সাহিত্যপাগল। আর অন্য দিকে মজলিশি। তার বাড়ির কাছারি ঘরে প্রায় প্রতিদিনই একেবারে নিয়ম করে জমজমাট সাহিত্যের আড্ডা বসত।
সেই আড্ডায় একটি অপরিচিত যুবকের ছিল নিত্য যাওয়া-আসা। পরনে হাঁটু ছুঁই ছুঁই খাটো ধুতি। গায়ে নিজের হাতে কাচা ইস্ত্রিবিহীন পাঞ্জাবি। এক হাতে লণ্ঠন, অন্য হাতে একটি লাঠি। এই যুবকটি তার জমাটি সাহিত্য জলসায় যেন শুধুই একজন শ্রোতা। যেমন নিঃশব্দে আসেন, তেমনি নিঃশব্দে চলেও যান। কত জন কত রকম আলোচনা করে। মন্তব্য করে। কিন্তু এই যুবকটি কোনও আলোচনাতেই অংশ নেন না।
বৈশাখ মাসের এক বিকালে হঠাৎ শুরু হল প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড়। আর সেই ঝড়ের জন্য সে দিনকার আড্ডায় উপস্থিত হল না প্রায় কেউই। উপেন্দ্রনাথ কাছারি ঘর থেকে নেমে মাঝে মাঝেই উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন, কেউ আসছে কি না। হঠাৎ রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখেন, দূরে একটি লণ্ঠনের আলো। সঙ্গে একটা ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তিটি এসে হাজির হলেন তার বৈঠকখানায়। আর তাকে দেখেই চমকে উঠলেন উপেন্দ্রনাথ। আরে, এ যে সেই যুবকটি! বিভূতি।
তার পর একেবারে পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসলেন বিভূতিভূষণ। উপেন্দ্রনাথ বললেন, এ কি, আপনি পেছনে বসলেন কেন? তিনি বললেন, আরও অনেকে আসবেন তো, আমি কি করে সামনের বেঞ্চে গিয়ে বসি! উপেন্দ্রনাথ বললেন, ঝড়-জল ভেঙে আজকে মনে হচ্ছে আর কেউ আসবে না। আসুন, আপনি সামনের চেয়ারটায় এসে বসুন। তার সঙ্গে নানা রকম গল্পগুজব করতে করতে উপেন্দ্রনাথ হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো প্রায় রোজই আমাদের সাহিত্য আড্ডায় আসেন। তা, আপনার কবিতা কিংবা গল্প-উপন্যাস লেখার কোনও বাতিক-টাতিক আছে নাকি?
বিভূতিভূষণ বললেন, না তেমন কিছু নয়, তবে একটা উপন্যাস লিখেছি। কিন্তু লেখাটি আদৌ পড়ার মতো কিছু হয়েছে কি না, বুঝতে পারছি না। উপেন্দ্রনাথ বললেন, তা হলে উপন্যাসের খাতাটি একবার নিয়ে আসুন। দেখি, কেমন লিখেছেন।
এ ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই বিভূতি তার পথের পাঁচালী উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি দিয়ে এলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। দিয়ে তো এলেন। কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ নেই। একদিন-দু’দিন করে কেটে গেল পুরো দুটো মাস। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ তাকে কিছুই বলেন না। বিভূতিভূষণ মনে মনে ভাবেন, তা হলে তার উপন্যাসটা কি আদৌ কিছু হয়নি!
একদিন মজলিস শেষ করে সবাই যখন একে একে চলে যাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে উপেন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণকে বললেন, আপনি যাবেন না। আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। সাহিত্য আসর থেকে সবাই চলে যাওয়ার পরে উপেন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণকে বললেন, ভাই আপনার হবে। হবে বলছি কেন? আপনার হয়েছে। কী এক অসাধারণ উপন্যাস লিখেছেন আপনি। পড়েই মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেছে আমার। যা হোক এ বার আসল কথা বলি, আমি ভাগলপুরে আর থাকছি না। কলকাতায় চলে যাচ্ছি। তবে আমার কলকাতায় যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেখান থেকে ‘বিচিত্রা’ নামে একটি পত্রিকা বের করার। সেখানেই আমি ছাপাব আপনার এই উপন্যাসটি। আপনার এই উপন্যাস দিয়েই যাত্রা শুরু করবে ‘বিচিত্রা’।
এর কিছু দিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করল বিচিত্রা পত্রিকাটি এবং বিভূতিভূষণের উপন্যাসও কিস্তিতে কিস্তিতে বের হতে লাগল। উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল, কে এই লেখক? যে এত দরদ দিয়ে সমাজ ও দেশ গ্রামের তুচ্ছ তুচ্ছ জিনিসগুলো এত মনোমুগ্ধ করে তার লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন?
এর কিছু দিন পরেই সে-সময়কার বিখ্যাত পত্রিকা ‘শনিবারের চিঠি’র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস অনেক খোঁজাখুঁজি করে তার ঠিকানা জোগাড় করে অবশেষে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। নব্বই টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, বিভূতিবাবু আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে পথের পাঁচালী উপন্যাসটি বই আকারে আমি ছাপব।
এর পর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ চলা কেউ আর থামাতে পারেনি। দু’হাতে লিখেছেন এবং যা লিখেছেন, তা প্রায় সবই জনপ্রিয় হয়েছে। বউয়ের মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বছর পরে তার পরিবারের লোকেরা তার আবার বিয়ে দেন। ১৯৪০ সালের ৩ ডিসেম্বর। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ছয়গাঁওয়ের ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে রমা দেবীর সঙ্গে। সেই বিয়ের সাত বছর পরে অবশেষে তার একটা ছেলে হয়। যার নাম ছিলো তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
‘পথের পাঁচালী’ তাকে এতটাই সাফল্য এনে দেয় যে, তিনি সেই কাহিনির এক্সটেনশন ঘটিয়ে আরও একটি উপন্যাস লেখেন। সেটার নাম অপরাজিত। এই দুটো উপন্যাসেই বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবনের বেশ খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।
সত্যজিৎ রায় এই ‘পথের পাঁচালী’ দিয়েই তার চলচ্চিত্র পরিচালনার জীবন শুরু করেন। আর এই ছায়াছবি তৈরি করার জন্যই ১৯৯২ সালে তিনি অস্কার পান। লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট। আর এই উপন্যাসটি ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তো বটেই, ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে।
পথের পাঁচালীর পরেই তার সব চেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস ‘চাঁদের পাহাড়’। মূলত ছোটদের জন্য লেখা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। যখন সুন্দরবনে যাওয়াও ছিল দুঃসাধ্য, সেই সময় একটা লোক আফ্রিকায় না গিয়েও, আফ্রিকার আমাজন জঙ্গল সম্পর্কে যে এ রকম জলজ্যান্ত বর্ণনা কী করে দিলেন, সত্যিই তা গবেষণার বিষয়। আর ‘আরণ্যক’? জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। খুব ছোট্টবেলায় বাবার হাত ধরে সেই যে তিনি বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতেন, গাছ চিনতেন, পাখি চিনতেন, পোকা-মাকড়-সাপ চিনতেন, তিনি যে শুধু চিনতেনই না, চিনতে চিনতে এই গাছপালা, পশুপাখি, আকাশ-বাতাস, মানে এই মুক্ত প্রকৃতিকে ভালওবেসে ফেলেছিলেন, তা তার আরণ্যক পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রকৃতিকে মনেপ্রাণে ভাল না বাসলে এ রকম একটা উপন্যাস কখনওই লেখা সম্ভব নয়। সব মিলিয়ে মনকে ছুঁয়ে যাওয়া এক অসাধারণ কাহিনি।
শুধু এগুলোই নয়, উনি যা লিখেছেন, সব ক’টাই একেবারে চমকে দেওয়ার মতো। তার লেখা বইগুলো মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- পথের পাঁচালি, অপরাজিত (১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৩২), আরণ্যক, আদর্শ হিন্দু হোটেল, ইছামতি, অশনি, জন্ম ও মৃত্যু, কিন্নর দল, বিধুমাস্টার, অসাধারণ, কুশল-পাহাড়ী, চাঁদের পাহাড়, অভিযাত্রিক, বনে পাহাড়ে, হে অরণ্য কথা কও’সহ প্রভৃতি।
এখানে যখন উপঢৌকন দিয়ে, একে-তাকে ধরে কিংবা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকার দরুণ কিংবা সরকারি বদান্যতায় এ, সে একের পর এক পুরস্কার বাগিয়ে নিচ্ছেন, বাংলা সাহিত্যে যে তিন জনকে ‘তিন বাঁড়ুজ্যে' বলা হয়, তাদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর এক বাঁড়ুজ্যে হলেন এই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কিন্তু তার জীবদ্দশায় একটাও সে রকম কোনও পুরস্কার পাননি। যেটা পেয়েছেন, সেটা তার মৃত্যুর পরে পেয়েছেন। ১৯৫১ সালে ‘ইছামতী’ উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। অবশ্য সব চেয়ে বড় পুরস্কারটাই তিনি পেয়েছেন, সেটা হল পাঠকের ভালবাসা, শ্রদ্ধা এবং সমীহ। একজন যথার্থ লেখকের কাছে এর থেকে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে! তিনি মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়সে, ১৯৫০ সালের ১ সেপ্টেম্বর (১৭ই কার্তিক ১৩৫৭, বঙ্গাব্দ, বুধবার) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঝাড়খন্ডের ঘাটশিলায় পরলোক গমন করেন।