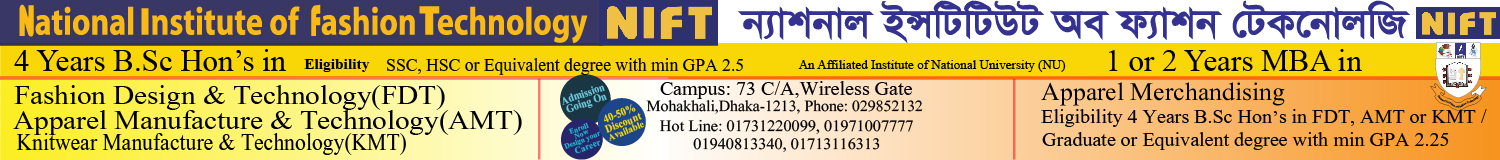অ-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানমনস্কতা
সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার
অস্ট্রিয়-ব্রিটিশ দার্শনিক কার্ল রেইম্যন্ড পপার (১৯০২-১৯৯২) The Logic of Scientific Discovery বইয়ে বিজ্ঞান সম্পর্কে খুব উত্তেজনাকর এক বক্তব্য দিয়েছিলেন ১৯৫৯ সালে। তিনি বলেছিলেন, “আমরা যাকে বিজ্ঞান বলে জানি, সেটা আদতে আমাদের কোন জ্ঞান দিতে পারে না; আমরা কোন কিছু জানতে পারিনা শুধু অনুমান করি মাত্র”। অর্থাৎ বিজ্ঞান প্রকারন্তরে একটা অনুমানমূলক বা আন্দাজে ধারণা ছাড়া বেশি কিছুনা। পপার আরো বলেন যে প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্য গড়ে ওঠে সেটার ভেতরেই রয়ে গেছে ফাঁক। যেমন যখন আমরা ধরে নিই “প্রতিটা তামার তার বিদ্যুৎ পরিবাহী” অথবা “সব রাজহাঁস সাদা” তখন মারাত্মক একটা পদ্ধতিগত ত্রুটির ভেতর আমরা ডুবে যায়, যার প্রেক্ষিতে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারিনা যে ঐসব কথাগুলো পুরোপুরি নিশ্চিত। তাছাড়া যেকোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নিয়ে সন্দেহ তো করাই চলে! বার্টান্ড রাসেল প্রবলেমস অব ফিলসফি-তে বলেছিলেন, “এ জগতে এমন কি জ্ঞান আছে যা নিয়ে কোন মানুষ কিছু না কিছু সন্দেহ করতে পারে না”? অন্তত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরকম কথা শুনতে মারাত্মক একটা খটকা লাগে নিশ্চয়।
সত্যি সত্যি বিজ্ঞানের জন্য এর থেকে মর্যাদাহানিকর কথা আর কী হতে পারে? বিজ্ঞান যেখানে ছোট্ট বালুকণা থেকে শুরু করে এই বিরাট মহাবিশ্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি চালিয়ে এর মর্মকথা উদ্ধার করে চলেছে সেখানে বিজ্ঞান আদৌ জ্ঞান দিতে পারে কিনা সেটা নিয়ে কেও যখন প্রশ্ন তোলেন, তা কতটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার সহজেই বোঝা যায়। অবশ্য পপার এহেন ‘ধৃষ্টতামূলক’ কথা বলেছেন একেবারে বিনা কারণে সেটা কিন্তু ভাববার কোন কারণ নেই। বিশেষত বিজ্ঞানের চরিত্র নিয়ে এধরণের কথা বলতে গেলে যে তার সমস্ত ইতিহাস হাতের মুঠোয় রাখতে হয়, সেটা বোধকরি পপার জানতেন। পপারের জীবদ্দশার প্রায় ১০০ বছর ছিল বিজ্ঞানের জন্য সবচেয়ে বিকশিত সময়। আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি কিম্বা কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে পপার প্রচুর ভাষ্য রচনা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। নিয়ন্ত্রণবাদ আর অনিয়ন্ত্রণবাদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আপেক্ষিক তত্বের ওপর চমৎকার একটা বই লিখেছিলেন The Open Universe নামে। পপার বিগত শতাব্দীর পুরোটায় বেঁচে ছিলেন আর সে সময় বিজ্ঞান কয়েক হাজার বছরের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল। পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, আর মহাকাশ বিজ্ঞানের চোখ ধাঁধানো উন্নতির এই সময়ে পপারের এই “আইকনক্লাস্টিক” ভাবনা যে ভীমরুলের চাকে ঢিল ছোঁড়ার মতো, সেটা আর নিশ্চয় মনে করিয়ে দিতে হবেনা।
এর প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীরাও কিন্তু কম যায়নি । টি. থিওচারিস এবং এম. সিমোপলাস নামে দু’জন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ১৯৮৭ সালে Where Science Has Gone Wrong ( Nature (vol.329, pp.595-598) নামে একটা গবেষণাপত্রে কয়েকজন “দুষ্টু” লোকের নাম করেছিলেন যারা সবাই ছিলেন ভীষণ নামকরা বিজ্ঞানের দার্শনিক। এঁরা হলেন কার্ল পপার, ইম্রে ল্যাকাটস, টমাস কুন, আর পল ফ্যায়ারাব্যান্ড। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো তাঁরা নাকি বিজ্ঞানের শত্রু, কারণ তাঁরা বিজ্ঞানের সব অর্জন আর ফলাফলের ওপর সবসময় সন্দেহ করে একটা বড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়ে রেখেছেন। বিষয়টা বড্ড গোলমেলে। কাজেই সহজে এর জট খুলতে আমাদের ফিরে যেতে হবে, সেই পুরনো প্রশ্নে। বিজ্ঞান আদতে কী? বিজ্ঞান কীভাবে অ-বিজ্ঞানের থেকে আলাদা। বিজ্ঞান আর অবিজ্ঞানের সীমানা নির্ধারণের পরিষ্কার কোন বিভাজন রেখা আছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি।
বিজ্ঞানের শুরুটা কবে হয়েছিলো তার পরিষ্কার ধারণা সম্ভবত নেই। কারণ মানুষ যখন গুহাবাসের আমল থেকে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বাঁচতে চেয়েছিল তখন থেকেই বিজ্ঞানের শুরু। বিজ্ঞান একটা পদ্ধতিতাত্বিক সুশৃঙ্খল বিশেষ জ্ঞান যার একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। এবং অবশ্যই সেটা পরীক্ষণ ও পরিমাপযোগ্য বিশেষ সম্প্রত্যয় যা দিয়ে মানুষ কর্ম সম্পাদন করে। আসলে বিজ্ঞান হলো প্রকৃতির নিগুঢ় ও গোপনে ঢেকে রাখা সত্য উন্মোচনের একটা সুশৃঙ্খল হাতিয়ার। এর দুটো মাত্রা আছে, একটা তাত্বিক অন্যটা ব্যবহারিক। ব্যবহারিক প্রেক্ষাপটকে বলা হয় প্রযুক্তি। কাজেই বিজ্ঞান শব্দটা প্রযুক্তির থেকে আলাদা করলে চলে না। বিজ্ঞানের তাত্বিক জ্ঞানটা যখন প্রয়োগের ভেতর দিয়ে কার্যকারী হয়ে উঠে তখনই সেটা প্রযুক্তির বারান্দায় গিয়ে পড়ে। কোন কিছুর পরিমাপ, দুরত্ব নির্ণয়, গ্রহগুলোর গতিবিধি, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি ছিল বিজ্ঞান শুরুর প্রথম পাঠ। তারও আগে বলা যায় যখন মানুষ পাথরে পাথরে ঘষা দিয়ে আগুন জ্বালাতে শিখেছে কিম্বা পাথরের মুখ সুচালো করে পশু শিকার করেছে তখনই বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তির শুরু হয়। পিথাগোরাসের সংখ্যার ধারণা, জ্যামিতিক উপপাদ্য, থেলিসের সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যৎবাণী এসব ছিল বিজ্ঞানের শৈশবযাত্রা। আর সেটা এখন থেকে আড়াই হাজার বছরের আগের কথা। যাইহোক খুব সঙ্গত কারণেই বলা যায় বিজ্ঞানের বাইরে যা আছে তাই অবিজ্ঞান। বিজ্ঞান আর অবিজ্ঞানের সীমানার মাঝে আমরা কীভাবে বিভাজন করি? দুটো দেশের মাঝে আমরা কীভাবে সীমানা টানি? দুটো জেলা বা উপজেলার মাঝে আমরা কীভাবে বিভাজন করি? খুব সহজ, ঢাকা জেলা শেষ হলে গাজীপুর ঢুকতেই সব জায়গায় লেখা গাজীপুর। আমরা যখন দেশের মানচিত্রটা হাতে নিই তখন দেখি একটা জেলা থেকে অন্য জেলার মাঝে একটা বর্ডার রেখা আছে। আসলে ওটাই বিভেদক রেখা বা বিভাজন সীমানা। তাহলে বিজ্ঞান আর অবিজ্ঞানের মাঝে এরকম একটা কিছু থাকবে নিশ্চয়। নিশ্চয় আছে। তবে গণ্ডগোল হলো, যে পরিষ্কার রেখা থাকার কথা ছিল দু’টোর মাঝখানে সেরকম কিছু পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আর এ জন্যই শুরু হয়েছে যত ঝামেলা। যেমন রংধনুর দিকে তাকালে আমরা সাতটা রঙের ধারাবাহিক সমাবেশ দেখি একের পর এক। কিন্তু সমস্যা হলো কোথায় বেগুনি শেষ হয়েছে আর কোন জায়গা থেকে নীল শুরু হয়েছে তার নির্দিষ্ট “কাটিং এজ” খুঁজে বের করতে গেলে গণ্ডগোল লাগে। ঠিক তেমনি করে নীলের শেষ, আসমানি শুরু; আসমানির শেষ সবুজের শুরু ইত্যাদি ইত্যাদি। অবিজ্ঞানের শেষ বিজ্ঞানের শুরু এমন রেখা তাই খুঁজে বের করাটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। শুধু কঠিনই না ভীষণ ঝক্কিরও। আর এই ঝক্কি নিয়ে বেঁধে গেছে ধুন্দুমার কাণ্ড। উপরে উল্লেখকৃত দু’জন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী যাদেরকে ‘দুষ্টু’ বলেছেন তাঁরা কিন্তু অনেক কিছুর মাঝে এই ধরণের বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসেছেন। যেমন পামিস্ট্রি বা হস্তরেখাবিদ্যা কোনোদিন বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারিনি। কারণ বিজ্ঞান যে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান দেয় এবং তার ভেতর যে অস্পষ্টতা থাকেনা সেটার মানদণ্ডে পামিস্ট্রি উৎরাতে পারেনি। মানুষের বিয়ে, উন্নতি, বিপদ, গ্রহের যোগ, শনির দশা, ইত্যাদি নিয়ে ভয়ঙ্কর গণ্ডগোলে সব কথা বলে হস্তরেখাবিদ তা কিন্তু বিজ্ঞানের জন্য বড্ড বেমানান। ঠিক তেমন করে ওঝা, তন্ত্রমন্ত্র, বানমারা, বাটিচালান, বশীকরণ আর যাদুবিদ্যা বিজ্ঞানের কাঠামো থেকে বাদ গেছে।
প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মানুষ এখন থেকে তিন, সাড়েতিন হাজার বছর আগে গণিত, মহাকাশবিদ্যা আর ওষুধবিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করেন। অবশ্য প্রাচ্যের মানুষও নাকি সমসাময়িক কালে এসব নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছিলেন। কোন কিছু “কেন” ঘটে, “কেন হয়”, “কেন অন্য কিছু না হয়ে এটা হয়”, “কেন চন্দ্র সূর্য মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ে”, “কেন দিন হয়, রাত আসে”, “এই বিশ্বজগতটার মূল উপাদান কী” ইত্যাদি সব “কেন” প্রশ্ন থেকে শুরু হয়েছে প্রাকৃতিক দর্শন তথা বিজ্ঞান। এই “কেন” প্রশ্নের আগে মানুষের মনের ভেতর ছিল বিশ্রী রকমের বাজে সব কল্পকাহিনী। এগুলোর বেশীর ভাগ ছিল বিশ্বসৃষ্টি, বীর আর নানারকম গ্রিক দেবতাদের শক্তির কথা। অনেকটা আমাদের দেশের জারি, গাজীর গান বা পালাগানের ঢঙে মানুষের মুখে মুখে হাজার বছর ধরে ছিল সেসব গল্পকথা। ট্রোজান ওয়ার এবং তার বিভিন্ন বীরদের সেসব গাঁথা নিয়ে হোমার কবিতার আকারে ইলিয়াড ও ওডিসিতে লিপিবদ্ধ করেন। হেলেন ও তার স্বামী স্পার্টার রাজা মেনেলাসকে ঘিরে নানারকম গল্প বানাতে গিয়ে যে কাহিনী বিস্তৃত হয়েছে সেগুলো এই ফিকশনের মূল বিষয়। হেসিয়ড দারুণ এক রোমাঞ্চকর বই যেখানে বিশ্বসৃষ্টির কথা, মানুষের দুঃখবেদনা, স্বর্গের কথা ইত্যাদি চমৎকার করে বর্ণনা দিয়েছেন হোমার। বলা বাহুল্য পাশ্চাত্যের জীবন ও সংস্কৃতির ওপর প্রাচীন মিথলজি ভীষণ প্রভাব ফেলে। সাহিত্য, চিত্রকলা, ও অন্যান্য শিল্পকর্মের মাধ্যমে গ্রীক মিথলজি প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য ভারতীয় মিথলজি তার অনেক পুরনো। খ্রিষ্টপূর্ব দেড় থেকে দুই হাজার বছর আগে বহিরাগত আর্যরা এখানে যে গ্রন্থ রচনা করেন যেসবের ভেতর ফুটে উঠেছে প্রাচীন ভারতীয় রূপকথা। তবে প্রাচিন ভারতের চার্বাক নামে একটা বিশেষ সম্প্রদায় ছিল দারুণ বিজ্ঞানমনস্ক যারা সবসময় শাসকশ্রেণীর তোপের মুখে পড়েছে।
এক্ষেত্রে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, অবিজ্ঞান বা মানুষের যুক্তিহীন বিশ্বাস থেকে বিজ্ঞান আলাদা হয়েছে একটা বিশেষ বৈশিষ্টসূচক বিভাজন রেখা দিয়ে যার নাম “পরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্ট”। আর এই এক্সপেরিমেন্টের প্রধান আশ্রয়স্থল হচ্ছে মানুষের ইন্দ্রিয়। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা হলো মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রধান উৎস, যা পরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণের ভেতর দিয়ে পরিপক্ক হয়ে ওঠে। সোনার ভেতরের খাঁদ যেমন এসিডের ভেতর দিলে পাকা হয়ে ওঠে অভিজ্ঞতার পুনঃপুন পরীক্ষায়ও তেমনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান খাঁটি হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের সত্য সম্ভবত এমন, “চিনিলাম আপনারে/ আঘাতে আঘাতে/ বেদনায় বেদনায়/ সত্য যে কঠিন/ কঠিনেরে ভালবাসিলাম”।
বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে। থেলিস, এনাক্সিমেন্ডার, এনাক্সিমিনিস এসব আইওনিয়ান দার্শনিকরা সবার আগে প্রশ্ন তোলেন এই জাগতিক বিশ্বের মূল উপাদান কী? কী দিয়ে তৈরি হয়েছে এই মহাবিশ্ব। কেও বলেছেন পানি দিয়ে, কেও আগুন, বাতাস ইত্যাদি। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এর কোনটাই পুরোপুরি সত্য না। কোনটা আংশিক, কোনটা কাছাকাছি আবার কোনটা মোটেও সত্যের ধারেকাছে না। তারপরেও এগুলোকে বলা হচ্ছে বিজ্ঞান। বলা হচ্ছে এ কারণে যে, বিজ্ঞান মানে চূড়ান্ত সত্য পাওয়া নয় বরং সত্য পাওয়ার প্রক্রিয়া। অর্থাৎ মনে রাখতে হবে, সত্য পাওয়ার জন্য গবেষক কী পদ্ধতি অনুসরণ করছেন? বিজ্ঞান অবিজ্ঞান থেকে আলাদা হয়েছে এই বিশেষ বৈশিষ্টের কারণে। তাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক পদ্ধতি হলো সবচেয়ে বড় ব্যাপার। মানুষের বিশ্বাস যখন বাস্তবতার সাথে মিলে যায় সেটাও সত্য বলে ধরে নেয়া যায়; কিন্তু সে সত্য পদ্ধতির পরীক্ষায় অনুউত্তীর্ণ। সুতরাং লক্ষ্য নয় বরং উপায় হলো বিজ্ঞান চিন্তার প্রধান বিষয়।
তবে সমস্যা দেখা দিয়েছে বিজ্ঞান অবিজ্ঞানের সীমানা নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছে বারবার, বিজ্ঞান যে পরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে; সবক্ষেত্রে কি এই বিভাজন সম্ভব হয়েছে? বিজ্ঞানে কি সবসময় অভিজ্ঞতার ওপর ভর করেই চলছে? বিজ্ঞানে কি অনুমান, কল্পনা, চিন্তা, আর গভীর অনুধ্যানের জায়গা ছিলনা? তাছাড়া বিজ্ঞান যে সমগ্রতার কথা বলে তাকে কি পুরোপুরি পরীক্ষা করা সম্ভব? সব রাজহাঁস কি একটা একটা করে দেখে বলা সম্ভব যে পৃথিবীর সব রাজহাঁস সাদা? যেহেতু কিছুসংখ্যক দেখে একটা সাধারণ অনুমানে আমরা লাফ দিই এজন্য “পরীক্ষা-নিরীক্ষার” যে তকমা বিজ্ঞানের শরীরে লেগে ছিল সেটা আর থাকলো কোথায়?
বিজ্ঞানের লম্বা ইতিহাসে সত্যিকার অনেক ঘটনা আছে যেটা বিজ্ঞানের সাধারণ চরিত্র বিরোধী। ১৮৯৯ সালে আগাস্ট ক্যাকুল বেনজিনের(C6H6) স্ট্রাকচার আবিষ্কার করতে গিয়ে যখন হিমশিম খাচ্ছেন তখন হঠাৎ তন্দ্রালু মুহূর্তে এক স্বপ্ন দেখেনঃ একটা অতিকায় অজগর সাপ কিছুটা বৃত্তের মতো হয়ে শুয়ে নিজের লেজ নিজেই কামড়াচ্ছে। তার কাছে মনে হয়েছে ঐ আকৃতিটা অনেকটা ষড়ভুজের মতো। পরক্ষনেই তিনি চিৎকার করে উঠে বলেন, “কোন সত্য পেতে গেলে আগে তার স্বপ্ন দেখতে শিখতে হয়”। স্বপ্নের সাথে সত্যের সম্পর্ক কী? ক্যাকুল বলেন, স্বপ্নের সাথে সম্পর্ক নিশ্চয় আছে। স্বপ্নই তো সত্যি। এ যেন গৌড়নন্দের কবির মতো, “জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়াময়/ স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়”। হেনরি পয়েনকেয়ার Science and Hypothesis বইয়ে লিখেছেন একটা বৈজ্ঞানিক সত্যে পৌছাতে গিয়ে হাইপথিসিস বা অনুমানমূলক চিন্তার কাঠামো খুব বেশি প্রয়োজন। তিনি লিখেছেন, “there are several kinds of hypotheses; that some are verifiable, and when once confirmed by experiment become truths of great fertility; that others may be useful to us in fixing our ideas;”।
আমরা শুরু করেছিলাম পপারের কথা দিয়ে। পপার কেন বিজ্ঞানকে কঞ্জেকচার বা অনুমানমূলক ভাবনা হিসেবে মনে করেন। পপারের এই ভাবনার একটা কারণ হলো বিজ্ঞানের ইতিহাস। বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে তিনি যে শিক্ষা নিয়েছিলেন তা কিন্তু বিজ্ঞানের জন্য সম্মানের কিছু নয়। বিজ্ঞান কি চূড়ান্ত কোন সত্য দিতে পারে? বিজ্ঞানের ইতিহাসে কি কোন ভুল-ত্রুটি নেই? বিজ্ঞনের দীর্ঘ পথে রয়েছে ভুল ভ্রান্তির চাদর বিছানো। তিনি মনে করেন বিজ্ঞানের সত্য চিরস্থায়ী না, কালের গর্ভে বিজ্ঞানের সত্য মিলে যায়, আবার নতুন সত্য জায়গা করে নেয়। এরিস্টটল আর টলেমীর বিজ্ঞান প্রায় হাজার বছর ধরে মানুষের মনোজগতে স্থায়ী জায়গা করে নেওয়ার পর সেটাকে উল্টে দেন কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও। আবার তাদের বিজ্ঞানও সময় গড়ালে পুরনো হয়ে যায়, আসে নতুন এক চিন্তা। নিউটনের মতো শক্তিশালী বিজ্ঞান যা আজও সমানভাবে কার্যকরী সেটাও আইনস্টাইনের কাছে এসে খাটো হয়ে যায়। এভাবে একটা প্যারাডাইম ছেড়ে অন্য একটা প্যারাডাইমে শিফট হওয়ার নাম বৈজ্ঞানিক বিপ্লব বা সায়েন্টিফিক রেভুলেশন। যখন চলমান বৈজ্ঞানিক তত্ব উদ্ভুত অবস্থা মোকাবেলা করতে হয় তখন একটা বৈজ্ঞানিক প্যারাডাইম পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়ে। এর প্রেক্ষিতে একটা বোধ দার্শনিক সমাজে বেড়ে ওঠে যে, বিজ্ঞানে চিরন্তন সত্য বলে কিছু নেই।
তবে মনে রাখতে হবে বিজ্ঞান চিরন্তন সত্য বলে কিছু মনে করেনা। আসলে চিরন্তন সত্য বলে আদৌ কিছু নেই। একটা সম্ভাবনার মহাবিশ্বে আমাদের বসবাস; আমরা চলেছি এক চলমান সম্ভাবনের রেলগাড়িতে। এই জটিল মহাবিশ্বের একটা একটা আবরণ খুলে তার ভেতরে প্রবেশ করার প্রচেষ্টাই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মানুষের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং কার্যকারণ চিন্তার প্রেক্ষিতে তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে একটা পরীক্ষণমূলক সিদ্ধান্তে পৌছাতে সহযোগিতা করে। ভুলে গেলে চলবে না বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন সপ্তদশ শতকের বিজ্ঞান অষ্টাদশ শতকের থেকে থেকে সীমিত, অষ্টাদশ শতকের বিজ্ঞান উনবিংশ শতকের থেকে বিজ্ঞান থেকে পিছিয়ে ইত্যাদি। এর অর্থ বিজ্ঞান চলমান এক জ্ঞানের পরিমার্জন। ক্রমবর্ধমান চেতনা ভাণ্ডারের হার না মানা পথ চলা। আগেই বলেছি সংশয় থেকে বিজ্ঞানের যাত্রা, সন্দেহ থেকে জ্ঞানের শুরু। বিজ্ঞানমনস্কতা মানেই সংশয়ী ভাবনা। স্থির, স্থানু ভাবনা কোন রহস্যকে উদ্ঘাটন করতে পারেনা। তবে আশার কথা মানুষ প্রকৃতিগত ভাবেই সংশয়ী; চেতনায় বিপ্লবী। আর একারণেই মানুষ জগতকে আজ এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। যদিও সাধারণ মানুষ জানেনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কী, তবু সে কিন্তু সমগ্র জীবন এই বিজ্ঞানের ভেতরেই বড় হয়। বিশ শতকের নামকরা কসমোলজিস্ট কার্ল সাইগান যথার্থ লিখেছেন, “we live in a society exquisitely depend on science and technology in which hardly anyone knows about science and technology”.
লেখক, সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
ওডি/